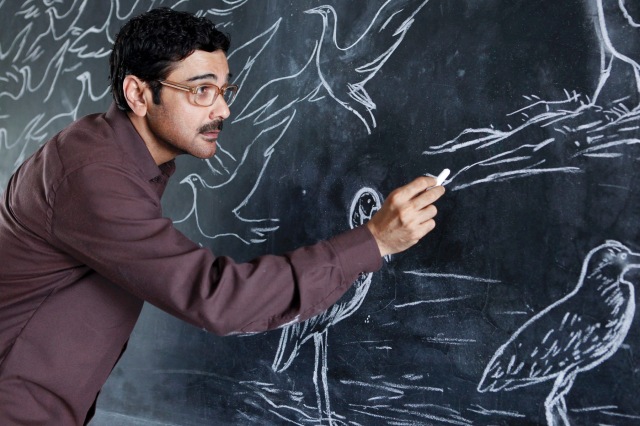প্রশ্ন : বাইরের দেশে বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, রাজনৈতিক সহিংসতার মতো ঘটনার কারণেই বেশী পরিচিত। সেখানে আপনার কেন মনে হলো একটা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মানুষের সংগ্রামই আপনার ছবির প্রধান বিষয় হতে পারে? আপনার কি কখনো মনে হয় নি যে এই ছবিটা বাইরের দেশের দর্শকদের কাছে একটা বাজে ধারণা দিতে পারে?
কামার আহমেদ সাইমন: একদম গোড়ার কথায় আসি। এ্যাস এ ফিল্মম্যাকার আমি একটা সহজলভ্য গল্পের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছিলাম কি না? যেমন ঐখানে মানুষ মারা গেছে ঐখানে ছবি হইতে পারে এমন কি না, খবরের মতো। আইলা হইছিলো মে মাসে। ঐ সময় আমি আমার একটা ফিচারের স্ক্রিপ্টের কাজ করছিলাম। আর ডিসেম্বর মাসে হইলো জলবায়ূ সম্মেলন। ঐখানে দেখি বাংলাদেশের অনেক বড় বড় লোক বিশাল আয়োজন কইরা যায়। আর আমি পত্রিকায় দেখি অন্য জিনিস, ছবি দেইখা আমার মনে হইতো যে শিল্পী এস এম সুলতানের ছবিতে যেমন মানুষের পেশীগুলো দেখা যায় ঐ রকম। রাত্রে মনে হইতো হাজার হাজার মানুষের পায়ের আওয়াজ পাই, মনে হইতো লাখো মানুষ ঢাকার দিকে আসতেছে! আমরা এত ইগনোরেন্ট, যে প্রায় দশ লক্ষ লোক মাসের পর মাস প্রায় বসে থাকলো, আর শহরে এইটা নিয়া কোনও হইচই নাই। ঐ অবস্থায় আউট অব কিউরিসিটি, আউট অব অ্যাঙ্গার কোনও রকম প্ল্যান ছাড়া আমি চলে গেলাম। এই যে আমি ঘোরাঘুরি শুরু করলাম, চললো প্রায় তিনমাস। ভোলা থেকে সাতক্ষীরা, প্রায় দুইশো কিলোমিটার, মূলত নৌকায়। কিন্তু ঐখানে গিয়াতো আমি বোকা হইয়া গেলাম। মনে হইলো আমি একজন শহরের মানুষ, একটা শহুরে টুপি পইড়া তাদের করুনা করতে গেছি। গিয়া দেখি আমি কোন ছাড়! শহর থেকে দূরে এই মানুষগুলি মাটির সাথে এত কাছে, তাঁর শেকড় মাটির ভেতর এত বেশী গভীরে যে সে কোনও কিছুর জন্যই আর অপেক্ষা করতেছে না। মানুষের যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, তার যে সংগ্রাম ঐটাই পুরা একটা সিনেমা। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চায়ের দোকানে বইসা বইসা আড্ডা মারি, এই কাজই করছি টানা প্রায় তিনমাস। ঐ সময় ঐ চাষি আমারে বলছিলো, আপনারা যারা শহরের মানুষ তারা এমন দূর্যোগে ত্রাণ না আসলে বিপদে পড়বেন। কিন্তু আমরা ঘটনার পর বাড়ি গিয়া দেখবো বীজ আছে কিনা, থাকলে প্রথমে তা লাগাইয়া দিবো। এই কথা শুইনা আমারতো মাথা ঘুইরা গেলো, মাথায় নেশা ঢুইক্যা গেলো! ফিরা আইসা ছোট ছোট করে লেখা শুরু করলাম, কোনও রকম পরিকল্পনা নাই, টাকা পয়সার কোন হিসাব নাই, পুরাই একা। কে দেখবে, কে দেখবে না… কে খাবে, কে খাবে না… এই চিন্তা ছাড়াই।
বাবু: তারেক মাসুদের ’আদম সুরতেও’ চাষীদের এমন কথা আছে।
কামার: হ্যাঁ আপনি ঠিক বলসেন। আমি তখন খালি সহজ মানুষের সাথে কথা বলি, আর প্রত্যেকবার নতুন নতুন কথা, সহজ কথা নিয়া ফেরত আসি। আর আইসা সারারে (সারা আফরীন, সিনেমার যৌথ নির্মাতা ও প্রযোজক) বলি, সারা এইখানে কি জানি একটা গল্প আছে। কল্পনায় মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের কুবের মাঝি আর তারাশঙ্করের কবির ছবি ভাসতে থাকে। চরিত্রগুলারেতো আর আমি দেখি নাই, কিন্তু ঐ সময় মনে হঠাৎ হঠাৎ হইতো আমার সামনে যেন কুবের মাঝি দাঁড়ায় আছে। আমার মাথাটা জাস্ট খারাপ হয়ে গেলো, ঐ সময় আমি গল্পের ভিতর ঢুইক্যা পড়সি। একভাবে বলতে গেলে গল্পটা আমি বাছাই করি নাই, বরং গল্পটাই আমারে বাছাই করসে! শিকার করতো গিয়া আমি নিজেই শিকার হইয়্যা গেসি। ছোট ছোট মানুষের অসীম সাহসের গল্প। বাইরের দেশে দর্শকরাতো ছবি দেইখ্যা সোজা হইয়্যা বসছে, আমারে বলে, ‘তুমি কি প্রোপাগান্ডা ছবি নিয়া আসছো? এই বাংলাদেশতো আমরা দেখি নাই!’ আমি হাইসা উত্তর দিসি, ‘আমিও আগে জানতাম না, এখন জানি আসলে… এইটাই আসল বাংলাদেশ।’
কমল : ছবির দর্শকের কমেন্টস যখন সরাসরি পাওয়া যায় তখন তো সেটা অনেক বড় অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে।
কামার : একটু আগে আমি এই অবজেক্টিভিটির কথা বলতেছিলাম না? মানে আপনি ছবি কেন বানাবেন? একজন ফিল্মমেকার হিসাবে আমি কিন্তু প্রচলিত অর্থে জাতীয়তাবাদী না। কিন্তু নিজের মাটির মানুষের গল্পে যে মজা পাই, মেকি কাহিনীতে সেই মজা কই? আমার ছবি সেই অর্থে হয়তো সফল নাও হইতে পারে, কিন্তু ছবি বানানোর একটা স্বার্থকতাওতো থাকা চাই, নাকি!
আমি: আসলে বিষয়টা এমন যে, আমরা সব সময়ই একটা চেইনের ভিতর জীবন যাপন করতে চাই। আমরা কখনোই এর বাইরের দিকটা দেখতে চাই না। ফলে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষের মতোই চলতে চেষ্টা করি, আমাদের ভেতর চেইনের বাইরে গিয়ে কিছু করার আগ্রহই নাই।
কামার: এইটা আমাদের সিস্টেমের দোষ। জন্মের পর থেকেই আমাদের ভিতর বিভিন্ন ভাবনা পুষ-ইন হইতে থাকে, চাহিদা পুষ-ইন হইতে থাকে। ক্লাসে ফার্স্ট হইতে হবে, কোরবানীর বড় গরুটা আমার চাই, দামী মোবাইল না থাকলে জীবন বৃথা… নানা রকম লোভ আমাদেররে সিস্টেমের ভিতর নিয়া আসে, একবার ঢুকলে বাইর হইতে কষ্ট আছে… কিন্তু অসম্ভব না।
প্রশ্ন: কেন ছবির নাম ‘শুনতে কি পাও’?
কামার: এই প্রশ্নটা আমার খুব পছন্দের। আপনি তো ছবিটা দেখছেন। ছবিটার এই যে চরিত্রগুলা রাহুল, রাখি, সৌমেনসহ একগ্রাম মানুষ… তাদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলো কি? এইটারে আমি মনে হইসে স্রেফ ‘সেলিব্রেশন অব লাইফ’ বা সহজ কথায় বলতে পারি ‘জীবনের জয়গান’। জীবনটা যে কত সুন্দর আর কত বিচিত্র, তা যে উদযাপন করা যায় তা আমি ঐখানে গিয়া রিয়ালাইজ করছি। আমিতো সেখানে প্রথমবার এক ধরনের রাগ নিয়া গেছিলাম, কিন্তু পরেতো আমি বোকা হইয়ে গেলাম। সহজ মানুষ, সত্য মানুষের যে কি সাহস, কি শক্তি সেইটা আমি ঐখানে গিয়া বুঝছি… শহরের মানুষ হিসাবে আমার যেইটার বরই অভাব! আমি যদি এই গ্রামটায় না যাইতাম, তাইলে আমার বোধটাই অপূর্ণ থাইক্যা যাইতো। একটা সময় এমন হইছে, আমি স্যুটিং থামাইতে পারতেছি না, একদম দিওয়ানা হইয়া গেলাম একরকম… মনে মনে ভাবলাম, জীবনের এই যে জয়গান আমি শুনলাম, সেইটা কি আমি দর্শকরে শুনাইতে পারবো? দর্শক কি শুনবে এই গান? আমি জানি না… তাই সেই থেকে নাম দিলাম, ‘শুনতে কি পাও!’
কমল : এই অবস্থায় এজ এ ফিল্মম্যাকার আপনার কাছে তথ্যচিত্রের মজা বেশী বলে আপনিই উল্লেখ করছেন। তো এই অবস্থায় আপনার কি ফিচার ফিল্ম বানানোর সম্ভাবনাটা আসলে কমে যাইতেছে?
কামার : আমি ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে ডকুমেন্টারি বানাই নাই। তাই আমি বোধহয় ঠান্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে ফিচারও মনে হয় বানাইতে পারবো না। আমি ঐভাবেই ছবিটা বানাইতে চাই যেইটা আমি ফিল করবো আমার মাঝে ভেতর থেকে। এই অবস্থায় আমার মনে হয় আমি যদি ডকুমেন্টারি বানাই, তবে তা ফিকশনের মতো হবে।
কামার : আপনার ছবির শুরুতেই আমরা দেখি রাহুল আর তার মা রাখীর একটা মানবিক অবস্থা তুলে ধরলেন। আবার একটা সময় গিয়ে দেখি গ্রামের মেম্বারকে জবাবদীহিতার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই যে মানবিক জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবনে গিয়ে আপনি দাঁড়াইলেন, এইটার সাথে সমাজ জীবনকে রিলেট করলেন কিভাবে?
কামার : দেখেন, আপনি শিল্পের যেই মাধ্যমেই চেষ্টা করেন আপনার ভেতরে যদি কোন সমাজদর্শণ কাজ না করে, ব্যক্তি মানুষের সংকট ও সামষ্টিক মানুষের যে দ্বান্ধিকতার মাঝে আমরা বাস করি… সেইটা আপনি যদি চ্যালেঞ্জ করতে না পারেন, তাইলে আর সিনেমা বানাইয়া লাভ কি? এরতো কোন অবজেক্টিভিটিই থাকে না!
কমল : ছবিতো শেষ পর্যন্ত একটা পণ্যও।
কামার : যেহেতু ছবি ভোক্তা খোঁজে… সেহেতু ছবি অবশ্যই পণ্য। সেই অর্থে কবিতাও তো পণ্য! তো এখন এই পণ্যের বাজারে এর ভেতর দুইটা একটা খোটা পণ্য তো থাকবেই, সময়-অসময়ের দাগ তাতে লাগবেই। সাদা চুল কালো করতে লাগে কলপ, কালো চেহারা ফর্সা করতে লাগে ক্রীম… জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে বুঝতে লাগে ছবি, জীবন ঘনিষ্ঠ ছবি। আসলে কি জানেন, কোনও সৎ শিল্প চেষ্টা কখনোই তার সময়টাকে অস্বীকার করতে পারে না। সময়ের দর্শন, রাজনীতি, সংকট… আর ব্যাক্তির জীবনে তার দ্বন্ধ চিরকালই ভালো শিল্প সৃষ্টি করেছে।
কমল : অসৎ শিল্প প্রচেষ্টা আপনি কোনটাকে বলছেন?
কামার : আমি যদি ছবিটা বানানোর প্রথম থেকেই ভাবতাম যে এইটা চলবে কি না? যদি ভাবতাম এইটাকে কিভাবে আরো চালানো যায়, আরো চালু জিনিস যেমন দারিদ্র, কান্না, দুর্যোগ ঢোকানো যায়… আপনিতো শুরুতেই আইলার কথা উল্লেখ করলেন, তো পুরা ছবিটাতে আইলার কিছু দেখছেন? এইখানে আইলা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, একটা উপলক্ষ মাত্র। ধরেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে প্রচুর ছবি হইছে, লাতিন আমেরিকার গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকট নিয়া কত ছবি হইছে। একজন সৎ নির্মাতার কিন্তু এইগুলা এড়াই যাওয়ার সুযোগ নাই। আপনার সামনে এমন ঘটনা ঘটতেছে অথচ আপনি একটু মশলা দিয়া চালু একটা সিনেমা বানাইলেন, এইটাই হচ্ছে অসৎ চেষ্টা। যেমন ধরেন, একাত্তর থেকে বাংলাদেশের চার দশকের সিনেমার কথাই যদি ধরি- প্রথম দশক এক ধরনের কুহেলিকার সময়ই গেলো বলতে গেলে। এক ধরনের নেতৃত্বহীন একটা অবস্থা। পরের দিকে দ্বিতীয় দশকে আলমগীর কবিরের মতো সিনেমা নির্মাতা আসলো। আশির দশকে শর্ট ফিল্ম ফোরামের মতো মুভমেন্ট, তারেক মাসুদ, তানভীর মোকাম্মেল, মোরশেদুল ইসলাম, জাহিদুর রহমান অঞ্জন, শারমিন আক্তারের মতো এক ঝাঁক নতুন নির্মাতারা এর মধ্য দিয়া আসলো। সেখান থেকে আপনি সুলতান (আদম সুরত), সেখান থেকে মুক্তির গান, পরবর্তিতে পাইছেন মাটির ময়না’র মতো ফিল্ম। এইটা গেলো দ্বিতীয় দশক, তৃতীয় দশকটা মানে নব্বইয়ের দশক আমার কাছে মনে হয় ফ্যাস্টিভ্যালের দশক। এখন আসি চতুর্থ দশক, শূণ্যের দশকে। ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে আমরা অনেক প্রমিজিং নির্মাতার কথা শুনলাম। যারা কমবেশী বিভিন্নভাবে ছোটবাক্সের হাতে একরকম অজান্তেই বন্দী হয়ে গেলো। অসাধারণ গুণী দু’একজন নির্মাতা যেমন সেলিম ভাই (গিয়াসউদ্দিন সেলিম), আতিক ভাই (নুরুল আলম আতিক), অনিমেষ আইচ এরা একের পর এক ভালো ভালো কাজ করলেও গড়পরতা নির্মাতাদের জন্য এটা অনেকটা দিন এনে দিন খাওয়ার মতো বিষয় হয়ে গেলো। ঐটা করতে গিয়া শূণ্যের দশকটা এক অর্থে অলমোস্ট গায়েব হয়ে গেলো। আপনি বলতে পারেন ২০০২ এ ‘মাটির ময়না’ হইছে, ‘মনপুরা’ হইছে। কিন্তু শুন্য দশকে এইগুলা নির্মাণ হইলেও এদের বীজ বপন ছিলো আশির দশকে। এখন এই শূন্যের দশকে শত শত তরুণ নবীন যারা আসলো, তারা এই প্রক্রিয়াগত সময়ে না ঢুইক্যাই, কর্পোরেট আর চ্যানেলের যোগসাজসে বিজ্ঞাপন আর নাটকের প্রোডাক্টিভ পাইপলাইনে ঢুইক্যা গেলো। এখন এইটাকে অসৎ বলবো না, কিন্তু শিল্পের এই বাণিজ্যিক চাপ যে খুব সৎ ছিলো তাও কিন্তু বলা যাবে না।
কমল: এইটা নিঃসন্দেহে হতাশার বিষয় যে, আমরা যাদের সম্পর্কে জানতাম এরা ভালো নির্মাতা হইতে পারে তাদের কাছ থেকে সিনেমায় তেমন কিছু আমরা পাই নাই।
কামার: দেখেন পাঁচজন নবীন নির্মাতা যদি এই দশবছরে দুইটা কইরা ছবি বানাইত পারতো, তাহলে আজকে আমাদের কাছে অন্তত বলার মতো দশটা নতুন ছবি থাকতো।
বাবু: আপনার ছবি দেশে প্রথমবারের মতো কোনও তথ্যচিত্র হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তিপেতে যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয়, আমাদের দেশের দর্শকরা একটা তথ্যচিত্র বাণিজ্যিকভাবে হলে গিয়ে দেখার মতো প্রস্তুত হয়েছে?
কামার: আমার ছবিটা নিয়া একটা মজার বিতর্ক চলতেছে। ডকুমেন্টারি নির্মাতারা বলতেছে এইটা ফিকশন, আবার ফিকশন নির্মাতারা বলতেছে ডকুমেন্টারি, আমি বলতেছি সিনেমা। আল্টিমেটলি এইটা কি সেইটা নির্ধারণ করবে দর্শক। আমি তাদের উপরই ছেড়ে দিবো বিষয়টা। দর্শক কিন্তু আসলে আগে থেকে নতুন কোন কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকে না, কিন্তু আপনি দিলে দর্শক কিন্তু ভালো মন্দ ঠিকই বুঝে… কম বেশি হয়, একটু সময় লাগে, এই আরকি।
কমল: এইখানে যেইটা হইছে বইলা কি আপনি মনে করতেছেন, যারা এই তর্কটা করতেছে তারা কেউ ছবিটার ভেতর ঢুকতে পারে নাই।
কামার: কিন্তু দর্শকের এই বিতর্কটা করার অধিকার আছে।
কমল: দর্শক তখনই যখন সে ছবিটা দেখবে। ছবি না দেখলে সে ছবির দর্শক না। তখন সে নিশ্চয়ই এইটা ডকু না ফিকশন সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারে না।
কামার: হ্যা, না দেখে কমেন্ট করলে সেটাও নির্মাতার প্রতি অন্যায় হবে।
কমল: দৈনিক পত্রিকা মারফত যখন আমরা এই ছবির খবর পাই, তখন আমি কিছুটা কনফিউজড। আসলে এইটা কি? ডকু না ফিচার এই বিষয় নিয়া আমার নিজেরো তখন কনফিউশন ছিলো।
কামার: কেউ যদি ছবি না দেখে এইটা ডকু না ফিচার সেই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় তারে অনগ্রসর দর্শক বলবো আমি। আমি মনে করি, একজন দর্শক ছবির মজাটাই দেখবে। এখন একজন দর্শকরে আমি আমার সিনেমার সামনে বসাইয়া দেয়ার পরে যদি সে ভিতরে না ঢুকতে পারে তাইলে আমি ফেইল্যুর, আর যদি আমি তার জীবন থেকে নব্বই মিনিট নিয়ে নিতে পারি তাহলে এইটা সিনেমা। সহজ হিসাব।
বাবু: ডকু ড্রামার যে বিষয়টা আছে, যেমন ধরেন নানুক অব দ্যা আর্থ কিংবা দ্যা লুজিয়ানো স্টোরি- ঐ রকম কিনা বিষয়টা?
কামার: সেইটা আমি কেন বলতে যাবো? সেটা দর্শকের সিদ্ধান্ত।
কমল: আপনার ছবির বিষয় যদিও দুর্যোগাক্রান্ত অঞ্চল, যদিও আপনার ছবিতে দুর্যোগটা মূখ্য বিষয় নয়, আপনি বলছেন যে আপনি শুনতে পাচ্ছিলেন দলে দলে মানুষ কাজের খোঁজে শহরের দিকে আসতেছে। তো আপনি যে ছবিটা দুর্যোগাক্রান্ত মানুষ নিয়ে বানাইলেন এর আগে আপনার কি কোনও রিসার্চ বা গবেষণা ছিলো না একদম মানবিক জায়গা থেকে ইনভল্ব হয়েই ছবিটা বানানো?
কামার: আগে থেকে কোন প্রস্তুতিই ছিলো না, আমি আমার ফিচার স্ক্রিপ্টে কাজ করতেছিলাম। এইটা এক ধরনের আলোর পোকার মতো। আমারে টেনে নিয়ে গেছে বিষয়টা।
প্রশ্ন: একটু আগেও উল্লেখ করছি আবারো তাই বলা, যে আপনার ছবির সফলতার খবর দিয়েই আমরা ছবি সম্পর্কে প্রথম জানি। তো আপনি প্যারিসে ‘গ্রাঁপি‘ পর্যন্তও পাইলেন আবার মুম্বাইয়ে ‘স্বর্ণশঙ্খ‘ও পাইলেন। তো আপনার ছবির এই সফলতা বাংলাদেশের ছবিতে কি প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন? আর একটু যোগ করি তারেক মাসুদের মাটির ময়না যখন কান ফ্যাস্টিভ্যালে গেলো সেখানে পুরস্কার পাওয়ার পর ছবির প্রতি মানুষের একটা আগ্রহ দেখা গেলো। তো এই ক্ষেত্রে আপনার ছবির এই সফলতা কোনও প্রভাব ফেলবে কিনা?
কামার: নিঃসন্দেহে তা দর্শকদের উপর প্রভাব ফেলবে। পণ্য যেহেতু তার ভোক্তার ওপর নির্ভরশীল। এখন পণ্যের চাহিদা তৈরির জন্য তো ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতেই হবে। তবে ‘গ্রাঁপি’ অথবা ‘স্বর্ণশঙ্খ’ পাওয়াসহ অন্য যে সব পুরস্কার আমরা পাইছি, তাকে আমি কাকতালীয় ছাড়া কিছু বলতে পারবো না। কারণ, যারা ছবিটা দেখবেন, তারা বুঝবেন ছবিটা পুরষ্কার পাবে এইটা মাথায় নিয়ে বানানো সম্ভব না। আমার ছবিটা যেখানে প্রিমিয়ার হইছিলো জার্মানির লাইপজিগে। পৃথিবীর প্রাচীণতম ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যালে উদ্বোধনী ছবি ছিলো এইটা। এরপর থেকে প্রায় বিশটার মতো ফ্যাস্টিভ্যালে যে গেছে তার সবগুলোই তাদের কাছ থেকে সরাসরি আমন্ত্রণে। আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, তারেক মাসুদের ‘মাটির ময়না’ যদি কান ফ্যাস্টিভ্যালে পুরস্কার না পাইতো বা আলোচিত না হইতো, তাইলে কষ্ট হইতো এইটা দর্শকদের কাছে নিয়ে যাইতে। পরবর্তীতে হয়তো দর্শক দেখে বলতো এইটা ভালো না, পুরস্কার ছবি সম্পর্কে এক ধরনের রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে। আজকে গার্মেন্টস শিল্পের দিকেই তাকান না কেন। একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী গর্ব বোধ করে যে আমি এক্সপোর্ট করি। আবার আপনি যখন এক্সপোর্ট কোয়ালিটির জিনিস কিনেন তখন আপনিও গর্ব বোধ করেন যে আমি এক্সপোর্ট কোয়ালিটির জিনিসটা ব্যবহার করি। হা হা হা
কমল: এই ছবি যদি ব্যবসায়িক ভাবে দর্শকদের মাঝে সাড়া ফেলতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের সিনেমায় কি প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন?
কামার: আমি তো মনে করি তরুণ যারা সিনেমা নির্মাতা আছেন বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতা, সংকটের কথা বলেন তারা আর এক্সকিউজ দেয়ার সুযোগ পাবে না। আমি যেই টাকায়, যেই সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে ছবিটার কাজ শেষ করছি এইটা যদি দর্শকরা নেয়… তাহলে তরুণ নির্মাতারা যারা ঘরে বসে নানা রকম স্বপ্ন দেখছে তারা ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস পাবে। তারা তখন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নক করবে। বলবে যে দেখেন এই যে আমার একটা সিনেমা আছে। এই সাহসটা কিন্তু খুব ইম্পোর্টেন্ট। আমরা কোনও কারণে এই সাহসটা পাচ্ছি না। সবাই আগেই ধরে বসে আছে, আমার ছবিটা বানাইতে পারবো না, বানাইলেও চালাইতে পারবো না, হবে না, ইত্যাদি। এই সংকটের মধ্যে আমি যে ছিলাম না তা তো না। তারেক মাসুদের এই সংকট ছিলো, আলমগীর কবিরেরও এইটা ডিল করতে হইসে, কিয়রোস্তামিও এর মধ্যেই বসবাস করে। এটা নির্মাতার জন্য নতুন কোনও সংকট না। কিন্তু এখন যদি এই ছবিটা দর্শকদের মাঝে সেই প্রভাব ফেলতে পারে তাহলে আপনার আমার মতো শত শত তরুণ যারা স্বপ্ন দেখছি ছবি বানিয়ে সমাজে পরিবর্তন আনবে সেই জায়গাটা অনেক বড় হয়ে যাবে।
কমল: আপনার স্যুটিং প্রসেসটা কেমন ছিলো?
কামার: প্রথম তিনমাসে আমি একটা লোকেশন, একটা গ্রাম আর চরিত্রগুলো নিশ্চিত করসি। তারপর থেকে ছয় মাস বলতে গেলে আমি এই ছয় মাস নিজের সাথে নিজের বোঝাপড়ার ভিতর দিয়া গেছি, একরকম সেল্ফ গ্রুমিং প্রসেসের মাঝ দিয়ে গেছি। কাস্টদের সাথে প্রতিদিন ওঠা-বসা করা, খাওয়া-দাওয়া করা, তাদের চরিত্রের সাথে মিশে যাওয়ার ভিতর দিয়া গেছি। এই সময়ে আমি দেখছি যে এই ছেলেটা এমন করে চলে এমন করে ক্যাপ পড়ে, তখন আমি তারে বলছি যে আমি যখন স্যুট করবো তখন তুমি কিন্তু দাঁড়ি রাখবা। তখন সে দাঁড়ি রাখছে। তবে আমি কোনও কিছু চেইঞ্জ করি নাই। এই রকম ছোট ছোট কাজ করে করে আমি ঐ লোকেশনটাকে গ্রুম করছি, ইউনিটকে গ্রুম করছি। পাশাপাশি এক ধরনের স্ক্রিপ্ট করছি। ছবির মাঝে একটা ন্যারেটিভ আছে, যারা ছবিটা দেখবে তাদের জন্য বিষয়টা ছবিতে আছে তাই এখন বলছি না। ছবির একটা জায়গায় গিয়ে যাত্রাটা শেষ হয়। এই যাত্রা শেষটা আপনি দুই বছর আগে প্রেডিক্ট করতে পারবেন না যে দুই বছর পরে এইটা হবে। এই ঘটনাটা পাঁচ বছর পরেও হইতে পারে, দশ বছর পরেও হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে। যেইটা আমি প্রেডিক্ট করছি যে এই পরিবারটা এরকম হবে, এই গ্রামটা এরকম হবে এই মানুষগুলো এরকম হবে। এইভাবে মানুষের বিভিন্ন চরিত্র আর দিনের গল্পকে চিন্তা করে ছোট ছোট সিকুয়েন্স লিখছি। যে চায়ের দোকানে এমন একটা বিষয় হবে, তারপর দেখলাম তাদের মধ্যে এই ঝগড়া হয়, বাচ্চাদের মধ্যে এই রকম কথা হয় এইসব আমি লিখলাম। এইসব করতে করতে যখন আসল স্যুটিংটা শুরু হইছে ততদিনে ছয় মাস কিন্তু চলে গেছে।
কমল: তাইলে প্রথম তিনমাসে আপনি গ্রামটা আবিষ্কার করলেন, পরবর্তি ছয়মাস আপনি আপনার গল্পের ধারাবাহিকতা আর চরিত্রগুলোকে সাজাইলেন। তারপর আপনি স্যুট করলেন?
কামার: এক্সেক্টলি। এই ছয় মাসও আমি ক্যামেরা নিয়ে গেছি। কিন্তু এই ছয় মাসের পর সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে আসছে। বলতে গেলে ফিকশনের প্রসেসেই এইটা করা হইছে।
বাবু: কত দিন স্যুট করলেন?
কামার: ঐ ছয় মাসসহ প্রায় বিশ মাসের প্রোডাকশন, যাওয়া আসার মধ্যে ছিলাম। কখনো চারদিনেই চলে আসতাম আবার কখনো টানা চার সপ্তাহও চলসে।
বাবু: ঐ আগের ছয় মাস প্রি-প্রোডাকশন হিসেবে কাজ করছে।
কামার: হ্যা, ঐ ছয় মাসকে প্রি-প্রোডাকশন টাইম বলা যায়। ঐ এলাকার ভাষাও তো শিখতে হইছে প্রথমে। আমার ছবির প্রত্যেকটা চরিত্রের ক্যারেক্টার সার্কেল আমাকে তৈরি করতে হইছে। এইসব করতে গিয়া আমি কখনোই ভাবি নাই যে ডকুমেন্টারি করতেছি না ফিকশন করতেছি। যতদিন আমার ভাল্লাগছে ততদিনই আমি স্যুট করছি। কারণ আমারে তো কেউ বলার কেউ নাই যে আপনি ডকুমেন্টারি বানাইতেছেন না ফিকশন বানাইতেছেন? আর আমি এইসব কেয়ারও করি নাই।
কমল: টিম ম্যানেজম্যান্টটা কেমনে করলেন?
কামার: টিম ম্যানেজম্যান্ট নিয়া আমার প্রচুর ভুগতে হইসে। প্রথমদিকে যখন কাজ শুরু করছি তখন অনেকেই খুব উৎসাহ নিয়া আসছে। ঐখানে কাঁদার মধ্যে বইসা খাওয়া দাওয়া, টয়লেট ছাড়া, যখন রাস্তার ওপর ঘুমানোর ব্যবস্থা দেখে তখন পরের দিনই সবাই পালাইয়া যায়। প্রত্যেকবারই আমি যাই আর প্রত্যেকবারই দুইটা একটা কইরা পালাইয়া যায়। আর যারা ফিরে আসে তারা ফোন ধরা বন্ধ কইরা দেয় এই রকম একটা কাণ্ড। এই রকম একটা পর্যায়ে আমার অনেক দিন গেছে। এই অবস্থায় গ্রামের কিছু ছেলেরে আমি ট্রেইন-আপ করে নিছিলাম। ওরা স্যুটিং এর প্রোডাকশন ম্যানেজম্যান্টটা শিখে গেছিলো। তারা জানে টাইম টেবিল কি, খাওয়ার শিডিউলটা কি হবে। ছয়টা সময় কল টাইম মানে ছয়টা সময় নৌকাটা ঘাটে রেডি থাকবে। এইভাবে ঐখান থেকে একটা লোকাল প্রোডাকশন ম্যানেজার হয়ে গেছে আমার। ঐখানে আমাদের একজন প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলো যে কিনা আমরা যাওয়ার আগে সবকিছু ঠিকঠাক করতো, একজন বাবুর্চি ছিলো সে রান্না করতো। ঐখানে তো ইলেক্ট্রিসিটি নাই। আমি ট্রাকের ব্যাটারি দিয়া আমি আইপিএস বানাইয়া নিয়া গেছি। একটা ছেলে ছিলো আমাদের জেনারেটর ঠিকঠাক করতো, আইপিএস রিচার্জ করতো। শেষের অংশটা ওরাই সাপোর্ট দিছে পুরাা।
বাবু: বাজেট কেমন ছিলো?
কামার : টোটাল ছবির? ছবির বাজেট তো এখনো চলতেছে। এই যে সিনেমা হলে যাওয়ার জন্যও তো আমার কাজ করতে হইতেছে। আমার এখন পর্যন্ত যে খরচ হইছে তা যদি আমি বলি তাহলে লোকজন আমাকে ভুল বুঝবে। দেশব্যাপী দেখাব বলে একটা ২কে এইচডি প্রজেক্টর কিনছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড়-যন্তর করে, অনেকের কাছ থেকে ধার নিয়ে, স্পন্সর নিয়ে। দেশব্যাপি দেখানো শুরু করব হোপফুলি ২১ শে ফেব্রুয়ারীর বসুন্ধরায় রিলিজের পর, এর জন্য আবার লাখ টাকা খরচা খরচ কইরা মুম্বাই থেকে ডিসিপি করে আনলাম। আমার খরচ হিসেবের বাইরে চলে গেছে। কিছু গ্র্যান্ট অ্যাওয়ার্ড পাইছি, সারা’র কিছু পারসোনাল সেভিংস ছিল, কিছু নানান জায়গা থেকে ধার করে, আমিও বলতে পারব না কত টাকা আসলে খরচ হইসে… কোটি ছাড়ায় যাবে। ফিকশনের ক্ষেত্রে বা নেক্সট প্রোজেক্ট যেগুলো করতেছি সেগুলো একদম প্রথম থেকে বাজেট করছি। এইটার সুবিধাও আছে, আবার অসুবিধাও আছে। আগে ফোঁড়া কাটা চিকিৎসক ছিলাম কেটে ফেলছি, (হাসি) এখন তো ফোঁড়া কাটতে পারছি না। এখন বসে বসে হিসাব করছি আর ভাবছি এইটা তো এই টাকায় হবে, ওই টাকায় হবে না।
কমল: আরেকটা বিষয়। ছবির টোটাল দুইটা জায়গায় আমি মজা পাইছি। সিনেমার যেই ইমেজ এবং সাউন্ড। আমার ধারনা ছবির পোস্ট প্রোডাকশন বেশ সময় দিছেন।
কামার: ইমেজে আর শব্দইতো সব… ইমেজে কালার গ্রেডিঙ্গ করা হইছে, সাউন্ড পোস্টে রিডিজাইন করা হইসে। এছাড়াতো আমি আপনারে এক্সপ্রেস করতে পারবো না, একটা উদাহরণ বলি… শুরুতে না দিন না রাত এমন একটা মুহূর্ত আছে ছবিতে। এখন উপন্যাস হইলে আপনি লিখে দিতেন, মাহেন্দ্রক্ষণ… অর্থাৎ না দিন, না রাত; আপনার কাজ শেষ মাত্র চার শব্দে। কিন্তু ছবিতে কিভাবে আনব, ছবির শুরুতেই আপনি একটা দৃশ্যে দেখবেন না দিন না রাত। আকাশে ছোট্ট একটা চাঁদ আছে, সেটা মেঘ আস্তে করে ঢেকে দিচ্ছে। এইটা তো দুর্ঘটনা না, তবে চাঁদটা মেঘ ঢেকে দিচ্ছে সেটাকে লাক বলতে হবে। জোয়ার ভাটা প্রতিদিন আধা ঘণ্টা করে শিফট হয়। এখন ঠিক সন্ধ্যার সময়, না জোয়ার না ভাটা এইটা প্রায় ২ মাসে একবার ঘটে। এর মধ্যে একটা অঙ্ক আছে। আমি দুই তিন বার ফেল করছি। আমি ৪টা থেকে শুট করছি, বিকাল সাড়ে পাঁচটা বাজে তখন পুরা পানি। আমি সেটা চাই নাই, আবার অন্য দিন সারে পাঁচটা বাজে পুরা শুকনা আমি সেটাও চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছিলাম একটু কাদা কাদা পানি। এর জন্য আমার টিম মেম্বাররা বিরক্ত হয়ে বলছে, আপনি কি শুরু করছেন? চার ঘণ্টা ধরে কয়বার স্যুট করব এইটা? আমি বসেছিলাম। ফাইনালি, আমি ওই শট টা পাইছি, এখন আমি আনন্দ নিয়ে আপনাকে এই কথাটা বলছি। এক্সিডেন্টালি পাওয়া সম্ভব না। সাউন্ড এ কাজ করতে গিয়া অনেক সাফার করছি, পরে লোকেশন থেকে রিকভার করার চেষ্টা করছি। আমি যে শব্দগুলো কানে নিয়ে ফিরত আসছি, সেগুলো আমি পাই নাই। সেগুলো আমার রি-এরেঞ্জ করতে হইছে। কিন্তু শব্দ বিষয় সিনেমার জন্য অনেকটা গন্ধের মতো, একটা বৃষ্টির শব্দ যদি কারেক্টলি হয় আপনার কিন্তু লোম দাঁড়াবে, সেনশেসন কাজ করবে। শব্দকে কোনভাবেই অবহেলা করা যাবে না। একটা খারাপ ইমেজের ভালো শব্দের ছবি কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন। কিন্তু একটা ভালো ইমেজের খারাপ শব্দের ছবি আপনি দেখতে পারবেন না। ওইটা ভেরি ইরিটেটিং। শব্দকে যতটুকু সম্মান জানানো যায়, সেটা চেষ্টা করছি, সাউন্ড এ এক্সপেরিমেন্ট করছি পুরো নেচারের সাউন্ড নিয়ে। বাতাস, আলো, সূর্য, পাতা এসব নিয়ে। যদিও ফাইনাল মিক্সিঙটা নিয়া এখনও আপত্তি আছে, যেমনটা ভাবছিলাম তেমন করতে পারি নাই, তবে ভুলের জায়গাগুলা আইডেন্টিফাই করসি, পরের কাজে লাগবে আশা করি।
কমল: আপনি বললেন যে, একটা মোমেন্ট এর জন্য ওয়েট করছেন কিন্তু পাচ্ছেন না, তখন কি আপনার হতাশা কাজ করছে?
কামার: ওরে… বাবা। (হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ )… পুরাটাইতো! এখন পর্যন্ত কষ্ট দেয় এরকম একটা আফসোসের কথা বলি। লোকেশান টা হল ভদ্রা নদীর পারে। আগেও দুই একজায়গায় বলছি, সারা (সারা আফরীন, প্রযোজক) জানে। আমি দেখতে পাই দূরে বৃষ্টি হচ্ছে, কালো হইছে। এবার মেঘটা ঘুরে ঘুরে নদীর উপর দিয়ে বৃষ্টিটা গ্রামটায় আসে। এইটা আমি কয়েকবার দেখছি কিন্তু শুট করতে পারি নাই। কয়েকবার চেষ্টা করেও নানান কারনে শুট করতে পারি নাই। আপনি দেখতে পাচ্ছেন নদীর উপর দিয়ে মেঘ এসে বৃষ্টি হচ্ছে। রুপালি নদিটা কালচে হয়ে গেছে, উপরে একটু ছায়া পড়ছে। নদীর উপর বৃষ্টি ঘুরে ঘুরে আসে সেটা আমি জানতাম না। এটা দারুন একটা ব্যাপার কিন্তু আমি শুট করতে পারি নাই। যারা ছবিটা দেখবেন তারা বুঝবেন, আমার মতো করে আমি বৃষ্টিকে ফিল্মের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করসি। ছবিটাতে বৃষ্টির কিছু কথা আছে, আশা করি দর্শকরা সেটা শুনতে পাবেন, বুঝতে পারবেন।
কমল: ছোটবেলা থেকে কোন সিনেমাগুলো আপনার উপর প্রভাব ফেলছে?
কামার: সিনেমার প্রভাব অনেক ছোটবেলা থেকে। মাথার মধ্যে একটা পোকা ঘুরতে ছিল, সেটা অনেকদিন ভোগাইলো। অনেকদিন সাহস দেয় নাই, অনেক দিন মনে হইছে আর হবে না। অনেকদিন মনে হইছে জীবন শেষ। এইভাবেই অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছি। অনেকগুলো সিনেমা আছে যেগুলো আমাকে সাহস দিছে। তার মধ্যে একটা হল, খুব পরিচিত ছবি আশা করি কম বেশি সবাই দেখছেন… সিনেমা প্যারাদিসো। আরেকটা হল কুরোসাওয়ার ড্রিম। আমার তো অনুভূতি আছে, আমি মানুষ তো। আমার তো সেনশেসন আছে। এই সিনেমা দেখে আগের মানুষটাই ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলে তো হবে না। এই সিনেমাগুলো দেখার পরে কিছু একটা হয়ে গেছে, ছবি কয়টাই এমন ছিল। কিন্তু ড্রিম ছিল শেষ সিনেমা যার প্রভাব আমার মধ্যে খুব বেশি কাজ করছে। আমার মনে হয় পৃথিবীর আল্টিমেট সিনেমাটা বানানো হয়ে গেছে এবং সেই সিনেমাটা দেখানো হয়ে গেছে। এখন যাই পারি ছবির ভাষায় যদি কিছু বলতে পারি।
কমল: আপনি যখন আর্কিটেকচার এ পড়াশোনা করতে গেলেন তার আগে থেকেই তো আপনার ভিতরে সিনেমার পোকা ঢুকছিলো?
কামার: একটা মজার ঘটনা বলি, এইচ.এস.সি. পড়ার সময় পাবলিক লাইব্রেরিতে ৭ দিনের একটা চাইনিজ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হইছিল। আমি একদম এক্সিডেন্টালি গেছি, ঠিক যেমন আমি সুতারখালিতে (শুনতে কি পাও-এর লোকেশন) গেছি। সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা টানা সিনেমা দেখলাম, ৭ দিন, একটাও সিনেমাও মিস করি নাই। মনে হইছে, আমার ফেইট (fate) আমাকে টান দিয়ে নিয়ে বসাইয়া দিছে, এটা এক্সিডেন্টালি! ক্যাফেতে তখন দশ টাকায় একটা তেহারি পাওয়া যাইত, সেটা খেয়ে আবার সিনেমা দেখতে যেতাম। অদ্ভুত সুন্দর সব ছবি, ‘ব্যালাড অফ এ ইয়োলো রিভার’, ‘রেড সোরগাম’… কোনটা কমিক, কোনটা এ্যাকশন, কোনটা রোমান্টিক। ওইটা ছবির জগতে প্রথম এ্যানকাউন্টার ছিল, এর আগে আমি ‘পথের পাঁচালি’ দেখছিলাম ক্লাস নাইন এ থাকতে। এবং ওটা যে ডোজ হয়ে গেছিল সেটা জানতাম না। তারপর বুয়েট-এ পড়ার সময় ক্লাস ফাঁকি দিয়ে টানা দেখলাম ঢাকার ফেস্টিভালগুলা।
কমল: আপনার সাথে তারেক মাসুদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক ছিল, আমরা কি ধরে নিবো আপনি তার দ্বারা অনুপ্রাণিত। এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন।
কামার: আমি তারেক ভাই দ্বারা শুধু অনুপ্রাণিতই না, তারেক ভাই না থাকলে আমি হয়তো ছবিতেই থাকতামই না। এর চেয়ে সহজ ভাষায় আর বলা যায় না। আমার মনে আছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এফডিসিতে গেছিলাম। তারপর যে কোন কারনে খুব সেন্টু (মানসিক ধাক্কা) খেয়ে বের হয়ে গেছিলাম। মনে মনে ভাবছি, আমি আর এই জগতে থাকব না। তারপর ইউনিভার্সিটি শেষ করে অনেকদিন পরে বলাকায় স্ক্রল দেখছি দেখছি মাটির ময়নার। তখন আমি সারাকে বললাম “সারা এই লোকটা কে?” এই লোকটার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তারপর মাটির ময়না দেখার পরে মাথায় আসলো, এই ছবি যদি বাংলাদেশে বানানো যায়? তার আগে কিন্তু সিনেমা করব না বলে সিদ্ধান্ত নিছিলাম। মাটির ময়না এত রেস্ট্রেইন এত শাটল ফিল্ম বানানো যায়! সেই ২০০২-এ তারেক ভাইয়ের সাথে তার বাসায় ঢুকলাম, তারপর ২০১১ এর ১২ অগাস্ট পর্যন্ত তারেক ভাইয়ের সাথে একটা যোগাযোগ ছিল। এমনকি ওনার মেইলের পাসওয়ার্ডও আমার কাছে ছিল, সম্পর্কটা এই রকম ঘনিষ্ঠ ছিল।
আরেকটা বিষয় কি এখন কেউ কেউ কিছুটা প্রশিক্ষণ নিয়ে, আবার কেউ প্রশিক্ষণ না নিয়েই ছবি বানাতে বাসছে। কিন্তু প্রশিক্ষণের বাইরে, টেকনিক্যাল বিষয়গুলোর বাইরে ক্যামেরা, এডিটিং, ম্যাক বুক, 7d, 5d এসবের বাইরে ছবি বানানোর মনস্তাত্ত্বিক যে জগতটা সেখানে আপনি যেই গানটা গাইবেন বা আপনি যেই সুরে গাইবেন সেটাও প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়াগত। যে জায়গা সেটা একটা মানুষের কোত্থেকে হচ্ছে বা কিভাবে হবে? এইটা দুইভাবে সম্ভব, এক হচ্ছে সে স্বশিক্ষিত হতে পারে যেমন বই পরে, সিনেমা দেখে, সরাসরি সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে, শিল্প আন্দোলন আরও অনেক আন্দোলনের অথবা ডিবেটের মাধ্যমে। আরেকটা হল গুরুমুখি শিক্ষা। একজনের সাথে থাকতে থাকতে তার জ্ঞানটা গ্রহণ করে…। এখন ঠাণ্ডা মাথায় যদি দেখেন আমাদের এখানে ষাট এর দশকে জহির রায়হান এর কথা এবং তার ‘কখনো আসে নি’ আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো ছবি। এবং ৭১’এ জহির রায়হানের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ছিলেন আলমগীর কবির এবং স্টপ জেনোসাইড এর ভয়েস ওভার-ও কিন্তু আলমগীর কবিরের দেওয়া। আলমগীর কবির তার মতো একটা জায়গা তৈরি করলেন এবং যেখান থেকে তারেক মাসুদের মতো নির্মাতারা তৈরি হলেন… এটা কিন্তু একদিনের যাত্রা না। আলমগীর কবির সূর্যকন্যা বানাইলেন ১৯৭৫ সালে আর শর্ট ফিল্ম ফোরাম এর প্রথম ফেস্টিভ্যাল হইল ‘৮৬ সালে। এইটা কিন্তু ১১ বছরের যাত্রা। তারেক ভাইদের সাথে পরিচয় ১৯৮১ সালে ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট নামে একটা সংঘটন করে ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স করাইছিলেন। প্রথম ব্যাচ এর স্টুডেন্ট ছিলেন এই তানভীর মোকাম্মেল, মোরশেদুল ইসলাম এবং তারেক মাসুদ এবং মানজারে হাসিন মুরাদ এরা সবাই। ৮১ সালে শর্ট ফিল্ম ফোরাম এর সাথে যুক্ত হওয়া, ১৯৮৬ সালে ফেস্টিভ্যাল করা। আদম সুরত নিয়ে প্রায় সাত বছরের যাত্রা, তারপর তার মুক্তির গান (১৯৯৬), তারপর মাটির ময়না (২০০২)। এই যে একটা মানুষের সময় পার হচ্ছে, এটা নির্মাতা হওয়ার প্রক্রিয়াগত জায়গা। উপায় কিন্তু দুইটার সম্মেলন, একটা পদ্ধতিগত আরেকটা গুরুমুখি। প্রক্রিয়াগত বিষয়ের মধ্যে যে বিচরণ এবং সেটার ঘঁষা-মাজা করে ট্রিম করে একটা গাছ তার আকার ধারণ করেন, গুরু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় যে ২০০২–১১ সাল পর্যন্ত তারেক ভাইকে সোজাসুজি বোঝার চেষ্টা করছি। তার চলচ্চিত্র ভাবনা, তার ফিলসফি, এসব বোঝার জানার চেষ্টা করছি। এবং সব সময় নিজেরটা দিয়ে সেটা কন্ট্রাডিক্ট করার চেষ্টা করছি, প্রশ্ন করছি, বিতর্ক করছি। এখন বিষয় হল, সেই যে লিগেসি’র জায়গা যেমন জহির রায়হান থেকে আলমগীর কবির আবার সেখান থেকে তারেক মাসুদ… আমার মনে নতুন প্রজন্ম এই বিশাল জায়গাটা মিস করছে।
কমল: বাবু একটা কথা বলে, সেটা হল আমরা হলাম এখন ডাউনলোড জেনারেশন…
কামার: আমি নেগেটিভ কথা বলতে চাই নি তবু আপনি প্রসঙ্গটা তুললেন… কাজের কথা হল আপনার চলচ্চিত্র ভাবনা, আপনার ফিলসফির জায়গাটা… সেটা তো খুলতে হবে, দরজাটা তো খুলতে হবে। আমার মনে হয় এখনকার তরুণ প্রজন্ম এই জায়গাটা ভীষন মিস করছে। এখন একজন তরুণ কি করে, একটা ক্যানন ফাইভ ডি ক্যামেরা আর ম্যাকবুক নেয়, তারপর শুট শুরু করে দেয়। এটা হল গিটার এ একটা কর্ড বাজানোর মতো, সম্মানের সাথেই বলি। একটা গিটারে কর্ড উঠানো আর একজন মিউজিক কম্পোজার হওয়া এক বিষয় না। দুইটা আলাদা ব্যাপার। আপনার ম্যাকবুক আর আপনার ফাইভ ডি মার্ক টু আপনারে ফিল্মম্যাকার বানাবে না। আপনি একটা গিটারে একটা কর্ড উঠাতে পারেন। খুব ভালো, কিন্তু আপনি যদি ওই ক্লাসিক্যাল প্রক্রিয়ায় আপনি নর্থ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল, নজরুলগীতির কথা বলেন, বাক এর মিউজিক এর কথা বলেন, ওই জায়গার মধ্য দিয়ে আপনি যত আলোড়িত হবেন- তত আপনার শিল্পবোধ, শিল্পের প্রকাশ, আপনার সৃষ্টি সেগুলো কিন্তু তত বেশি চ্যালেঞ্জড হবে, দর্শকের ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু আপনি একজন নির্মাতা হিসেবে সারাক্ষণ খেলতে পারবেন। সেই খেলা এবং মজা দুইটাই মিস হয়ে যাচ্ছে। হয় খুব বেশি এক্সপেরিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছে ডিসকানেক্টশন এর কারনে। নতুন প্রজন্মের লোকেরা আলমগীর কবির সম্পর্কে জানেই না। অথচ আলমগীর কবিরের সিনেমা ‘সূর্যকন্যা’, বা জহির রায়হানের ‘কখনো আসেনি’ বা তারেক মাসুদের ‘অর্ন্তযাত্রা’… এগুলোর মধ্যে যে মজা আছে আপনি কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় দেখতে পারবেন না। সূর্যকন্যায় ১৯৭৫ সালে বানানো যে অপটিক্যাল এনিমেশন আছে সেটা ভাবাই যায় না, নির্মাতা কতটা মডার্ন ছিলেন।
বাবু: নারীর ক্ষমতায়নের যে জায়গাটা?
কামার: নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারটাকে কিন্তু একটু লাউডলি দেখা হচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে উনি নারীবাদি ছিলেন… ওসব কিছু না, আরে ভাই সহজ কথায় উনি মানবতাবাদি নির্মাতা ছিলেন। উনি একটা ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন তুলছিলেন… যে সমাজের পত্তন হইছিল মাতৃতান্ত্রিক হিসাবে সেটা পিতৃতান্ত্রিক কিভাবে হইলো! কিন্তু এখন আমরা কিভাবে ইম্বেল্যান্সড হয়ে গেছি। ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার… একটা চরিত্রের সঙ্কট থেকে তার মগজের ভিতরে প্রবেশ করে একটা এনিমেশন করে একটা হিস্টরি দেখাইয়া দিছেন, দেখলে মনে হয় এখনকার ছবি। একটা জায়গায় ক্যামেরার অস্থিরতা, এখন আমরা ক্যামেরার ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কত কথা বলা হয়। হ্যান্ডহ্যাল্ড ক্যামেরা কাকে বলে, ১৯৭৫ সালে কেউ জানতো? উনি গল্পের প্রয়োজনে হ্যান্ডহ্যাল্ড ক্যামেরা ব্যাবহার করছে সেই ‘৭৫ সালে। সেই সময় ৩৫মি.লি. ক্যামেরার ওজন ছিল প্রায় ৪০ কেজি। সেইটা নিয়ে দৌড়াইছে। আপনি সেই শটটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। কত রকম এক্সপেরিম্যান্ট করছেন। এখনও আমি অবাক হয়ে যাই ‘কখনো আসেনি’ সিনেমা দেখলে। এই ফিল্মটাতে কতগুলো ক্যামেরার কাজ আছে। কতগুলো কনসেপ্ট এর যায়গা আছে। আমার ফাইভ ডি, কিংবা ম্যাকবুক আমারে এই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখাবে না। টেকনোলজি আপনাকে টেকনিক শিখাবে, যেটা চলচ্চিত্র নির্মাণে অপরিহার্য। কিন্তু যে সিনেমাটা আপনি বানাবেন সেই ভাষাটাতো আপনার প্রথমে শিখতে হবে। আপনি বাম আন্দোলন করেন, আর ডান আন্দোলনই করেন, আপনাকে একটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাইতে হবে… মানুষ হইতে হবে তো প্রথমে।
কমল: এখন ছবি মুক্তি দেওয়ার বিষয় ছাড়া আর কি নিয়ে কাজ করছেন?
কামার: আমি এইমুহূর্তে একটা ফিচারের স্ক্রিপ্ট লেখা আর দুইটা ডকুমেন্টারি’র রিসার্চ ডেভেলপম্যান্ট লেভেলে আছি। এই তিনটা ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। কিন্তু এই ছবি মুক্তির বিষয়টা ঠিক হওয়ার পর থেকে বাকি সব বন্ধ করে এইটা নিয়েই আছি। অন্য কিছু করা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না।
কমল: আমাদের বাংলাদেশের ফিল্মে সামগ্রিক ইন্ডাস্ট্রির যে অবস্থা অর্থাৎ এফডিসির ছবি, বাইরের ছবি, বা বড় প্রোডাকশন হাউজের ফিল্ম এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম আবার এফডিসির বাইরের ফিল্ম হলেই সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে না। কারন এখানে কিছু বড় বড় প্রডিউসারদের ফিল্ম আছে। যদিও আপনারটা একটা ইন্ডিপ্যান্ডেন্ট ফিল্ম। এখন বাংলাদেশের ফিল্ম এর বতর্মান অবস্থা এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার কি অভিমত কি?
কামার: আমি দুঃখিত কারণ এইখানে আমি পজেটিভ কথা বলতে পারব না। কিছু নেগেটিভ কথা বলতেই হবে। আমি প্রতিদিন খুব ভয়ঙ্কর একটা আশঙ্কা নিয়ে ঘুমাতে যাই যে আগামি দুই- চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশের পুরো চলচ্চিত্র বাজারটা সিনেমা হলসহ বিদেশীদের দখলে চলে যাবে। এইটা অনেকখানি গেছে, ডাউনলোড বা পাইরেটেড এর মাধ্যমে আমার দর্শক অলরেডি বিদেশী সিনেমার ভোক্তা হয়ে গেছে। এর জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত বিভিন্ন মিডিয়াকে। যারা আমাদের মধ্যে ইনজেক্ট করছে ক্যাটরিনা কাইফ থেকে শুরু করে এঞ্জেলিনা জোলি সবাইকে। কে কোথায় বিয়ে করে, কে আংটি পরে, কে তার বাচ্চার নাম কি রাখছে। এসব দ্বারা ইনজেক্ট হয়েই এখনকার তরুন প্রজন্ম দিন যাপন করে। সিনেমাহল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম পায়তারা বিভিন্ন রকম আওয়াজ পাই যেটা আমাকে বলে যে আগামি ২/৪ বছরের মধ্যে পুরো ব্যাপারটাই দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। দেউলিয়া হওয়ার বিষয়টা দুইভাবে ঘটতে পারে। একটা হল আপনি সরাসরি বিদেশের ছবি এনে চালাইয়া দিলেন আর অন্য একটা হল আপনি বিদেশি ছবির রিমেইক চালানো শুরু করলেন। দুইটাই কিন্তু দেউলিয়া হওয়া এবং দ্বিতীয়টা কিন্তু অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে, এবং একটা কম্পিটিশন চলতেছে কে কার চেয়ে বেশি দেউলিয়া ছবি বানাইতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই যখন এইটা ফেল করে যাবে তখন সরাসরি বিদেশি ছবি প্রবেশ করবে। যখনই রিমেকটা পুরো ফেল করবে তখনই সরাসরি বিদেশি ছবি চলতে শুরু করবে। এখন যেই দাবাং সিনেমা এখানের হলে রিমেক টা চলতেছে পরে দেখবেন মূল দাবাং এখানে চলতেছে। এইটা একটা বিরাট সঙ্কট মনে হয় আমার কাছে। তবে আমি আরেকটা দিকে খুব আশাবাদী এই কারনে যে এখন তরুণ দর্শক এবং তরণ নির্মাতা, তরুণ চলচ্চিত্র কর্মী এবং সরকার মহোদয় সবার যদি একটা সদিচ্ছা থাকে, তাইলে যদি প্রোপার ফিল্ম পলিসি করা যায়। তাইলে আমরা পুরো বিষয়টা আমাদের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারি। বিদেশি সিনেমা থামানোর দরকার নেই, আমি বিদেশি সিনেমা থামানোর পক্ষে না, আমি একটা সঠিক রেগুলেশন এর পক্ষে। যার মাধ্যমে আমার ঘরে বৃষ্টি আসলে আমি জানালাটা বন্ধ করে দিতে পারি। এই ব্যবস্থাটা থাকলেই চলবে। এখন আমরা পুরো সিনেমার বাজার উজাড় করে দিয়ে বসে আছি। সেইটা যেন না ঘটে, যা আমাদের টিভি এর ক্ষেত্রে হইছে। এইটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের দোষে হইছে, এখন আমরা বলি আমাদের চ্যানেল দেখায় না, শুধু ওদের চ্যানেল দেখায়। এটা ডিস্ট্রিবিউটরদের ব্যর্থতা। সবাই বলতেছে দর্শক কেন বিদেশি চ্যানেল দেখে? এই বিষয়টা এখন চলচ্চিত্রেও ঘটবে। কিন্তু তরুণ দর্শক এবং তরুণ নির্মাতা, তরুণ চলচ্চিত্র কর্মী এবং সরকার মহোদয়ের যদি সদিচ্ছা থাকে তবে পুরো ব্যাপারটা আমাদের চলচ্চিত্রের জন্য পসেটিভ টার্ন নিতে পারে।
কমল: আপনি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে একজন আর্কিটেক্ট কিন্তু এখন আপনি একজন ফিল্মম্যাকার। যদি এর মধ্যে কোনটাই না হতেন তবে কি হইতেন?
কামার: আমি তো এতক্ষন ধরে এইটা ভালো আলাপ আলোচনা ভাবছিলাম। কিন্তু এখনটা আপনি কসমেটিক আলোচনার দিকে চলে গেলেন! হা হা হা আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হত তবে আমি বাঁশি বাজাইতাম। আমাকে যদি ঈশ্বর একটা সুযোগ দিয়ে বলে যে, তুমি কি হইতে চাও? আমি বলতাম, ‘আমি ক্ল্যাসিক্যাল ফ্লুট বাজাইতে চাই… শুধুই নিজের জন্য।’ মাঝে মাঝে যেসব কিছু বাজনা শুনি, মনে হয় যেন আমারই কান্না কেউ বাজাইতাছে। গত কয়েকদিন দিন ধরে একটা পিস (রুদ্রবিনা) প্রতিদিন সকালে তিন চারবার শুনতেছি। এত সুন্দর বাজাইছে বাহাউদ্দিন ডাগর, মনটা অনেক খারাপ হচ্ছে।
কমল : অনেক কথা হল আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।
কামার : আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ।